Tore Janson-এর সুইডিশ ভাষায় রচিত Latin: Kulturen, historien, språket গ্রন্থের Merethe Damsgård Sørensen ও Nigel Vincet-কৃত ইংরেজি অনুবাদ A Natural History of Latin-এর বাংলা ভাষান্তর
দর্শন : লুক্রিশাস, সিসেরো আর সেনেকা
‘Philosophy’ শব্দটা গ্রীক; মানে অনেকটা, ‘প্রজ্ঞাপ্রেম’। গ্রীকদের কাছে কথাটার অর্থ ছিল যা কিছু সত্য আর সঠিক তার জন্য সর্বোচ্চ রকমের পদ্ধতিগত অনুসন্ধান। আমাদের সবারই জানা আছে দর্শনের জগতে তারা পরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল, আর তাদের সেরা দার্শনিকেরা, যেমন প্লেটো এবং এরিস্টটল, যা লিখে গেছেন তার অনেকটাই এমনকি আজও তার তাৎপর্য ও গুরুত্ব এতটুকু হারায়নি।
রোমক দর্শন গড়ে উঠেছিল পুরোপুরি এই অসামান্য গ্রীক দার্শনিক ঐতিহ্যের ওপর ভর করে, যেখানে আমরা দেখতে পাই এই জগৎকে জানার, ব্যাখ্যা করার এবং কিভাবে জীবন যাপন করা উচিত তার দস্তুর ঠিক করার বিচিত্র প্রচেষ্টা। নতুন দার্শনিক ধ্যান-ধারণা রোমকরা বেশি কিছু প্রবর্তন করেননি, তবে তাঁরা গ্রীকদের চিন্তা-চেতনা লাতিনে স্থানান্তর করেছেন, আর তা করতে গিয়ে সেসবে অল্প-বিস্তর পরিবর্তন এনেছেন।
সে যাই হোক, রোমক দার্শনিকেরা দুটো কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, তাঁরা গ্রীক দর্শনের সার কথাটি লাতিন-জানা সবার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, যা ইউরোপীয় চিন্তার পরবর্তী ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। আর দ্বিতীয়ত, তৎকালীন দর্শনগত যুক্তিবিচার পদ্ধতির (philosophiical reasoning) প্রতিশব্দ তৈরি করেছিলেন তাঁরা যা অসংখ্য তাৎপর্যপূর্ণ মৌলিক চিন্তাবিদেরা ব্যবহার করেছেন এবং লাতিনে তাঁদের ধ্যান-ধারণার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, প্রাচীন কালের শেষাংশের অগাস্টিন এবং নানান খৃষ্টীয় আচার্য থেকে শুরু করে ১৭শ শতকে দেকার্তে এবং স্পিনোযা পর্যন্ত।
লাতিনে লেখা প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক রচনাটি পরবর্তীকালেও বেশ প্রভাবসঞ্চার করেছিল। সেটার নাম, ‘De rerum natura’, বা, ‘বস্তুর প্রকৃতি প্রসঙ্গে’, রচয়িতা লুক্রিশাস (Lucretius) যিনি ৫৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এই রচনাটি কাব্যিক ধারা বা ঐতিহ্যেরও অন্তর্ভুক্ত, কারণ এটি একটি দীর্ঘ ষটপদী উপদেশাত্মক কবিতা; ভার্জিল তাঁর ‘ঈনীড’ মহাকাব্যেও একই মাত্রা ব্যবহার করেছিলেন। গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাসের (Epicurus) প্রবল অনুরাগী ছিলেন লুক্রিশাস। আজ মানুষ এপিকিউরাস বলতেই আনন্দই পরম মঙ্গল বা শুভ, এই নীতির প্রবক্তাকে বোঝে; আর তাই আনন্দপ্রেমী মানুষকে কখনো কখনো এপিকিউরীয় বলেও অভিহিত করা হয়।
কিন্তু তাঁর দর্শনের এই দিকটি নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না লুক্রিশাসের। তাঁর দৃষ্টিতে এপিকিউরাস ছিলেন সেই মানুষ যাঁর তাকদ ছিল পরমাণুবাদী তত্ত্বের সাহায্যে যুক্তিসিদ্ধভাবে — অর্থাৎ দেবকুল ও নানান অজ্ঞাত শক্তি সম্পর্কে যাবতীয় ভীতি ঝেঁটিয়ে বিদায় ক’রে — গোটা জগৎকে ব্যাখ্যা করার। কবিতার প্রায় শুরুতে একটি পংক্তি দেখতে পাই আমরা :
‘religio potuit suadere malorum’, মানে, ‘তো, ধর্ম এই পরিমাণ অমঙ্গল ঘটাতে পেরেছে’। লাতিন শব্দ বিন্যাস অনুযায়ী কথাটা হবে, ‘ধর্ম-এই-পরিমাণ-করতে-পেরেছে-অমঙ্গল’।
বস্তুর প্রকৃতি বিষয়ক রচনাটি ছয়টি বই বা পর্বে বিভক্ত, প্রতিটিতেই রয়েছে সহস্রাধিক পংক্তি বা চরণ। প্রথম দুই পর্ব পরমাণু এবং কি করে জগতের সব কিছু তা দিয়ে গড়ে উঠল আর কি করেই বা শেষঅব্দি সব কিছু ভেঙেচুরে সেই পরমাণুতেই ফিরে যায় তাই নিয়ে। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব আত্মা, ইচ্ছে, এবং সংবেদন বা বোধ নিয়ে; আর সেখানে, আমাদের যেসমস্ত অভিজ্ঞতা হয়, আমরা যা অনুভব করি সেসম্পর্কে বস্তুগত ও যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্ব মহাজগৎ আর মানুষের ওপর যেসমস্ত বাহ্যিক শক্তি কাজ করে, যেমন খারাপ আবহাওয়া ও অসুস্থতা, এসব নিয়ে। এখানে প্লেগ বা মহামারীকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে মন্দ বায়ু এবং কোনো সংক্রমণের পরিবহন হিসেবে, যার সঙ্গে মানুষকে দেবতাদের দেয়া শাস্তির কোনো সম্পর্ক নেই। আর পুরো রচনাটি শেষ হয়েছে এই ধারার যুক্তির একটি অসাধারণ চিত্র দিয়ে, এথেন্সের প্লেগের এক সাড়ম্বর ও বুক কাঁপানো বর্ণনার মাধ্যমে।
অবশ্য, কবিতাটির বাকি অংশে লুক্রিশাস ঠিক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে সেরকম যুতসই উদাহরণ বা সমান্তর কিছু দেখাতে পারেন নি। স্বভাবতই, রচনাটির একটা বিরাট জুড়েই রয়েছে দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, যদিও তা করা হয়েছে পদ্যে। মাঝে মাঝে তিনি পড়ে যান, গ্রীক বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকে লাতিনে স্থানান্তর করার সমস্যায় পড়ে যান, আর তা নিয়ে আসলে অভিযোগও করেন। এ পর্যায়ে এসে কথা বলেন ‘patrii serrmonis egestas’ বা, ‘আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ভাষার দারিদ্র্য’ নিয়ে। কাজেই, পুরোপুরি সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বললে বলতে হয়, টেক্সটটি বরং অমসৃণ। কিছু কিছু অংশ — যেমন ভূমিকাটি লাতিনে যা কিছু রচিত হয়েছে তার মধ্যে সেরা, এবং লাতিন কাব্যের মহান শিল্পী ভার্জিল লুক্রিশাস পড়ে অনেক কিছু শিখেছেন। কিন্তু সে তুলনায় অন্যান্য অংশ রসকসহীন বেশ। অবশ্য, এ-কথাও আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে নেহাত শিল্পসৃষ্টি এ-কাব্যরচনার উদ্দেশ্য ছিল না মোটেই। লুক্রিশাস ছিলেন লাতিন ভাষায় এপিকিউরাসের এক দূত, আর তাঁর মূল আবেগের জায়গাটি ছিল মানুষকে একথা হৃদয়ঙ্গম করানো যে, জগৎ আসলে অনুধাবনযোগ্য বা বোধগম্য কিছু প্রাকৃতিক শক্তির বলে চলে। বিজ্ঞান, বস্তুবাদ আর যুক্তিবাদের বার্তাবহ ছিলেন তিনি।
তবে দীর্ঘ একটা সময় যেন তাঁর সেই বার্তা পৌঁছয়নি জায়গামতো। রোমে খুব বেশি মানুষ যে তাঁর লেখা পড়তো তা নয়, আর মোটের ওপর দায়িত্ব ও ধার্মিকতার বৈরাগ্যদর্শন সংক্রান্ত আচরণবিধি (Stoic ethic) এপিকিউরাসের দর্শনকে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল। বৈরাগ্যদর্শনের বেশিরভাগ ধ্যান-ধারণাই গ্রহণ করেছিল খৃষ্ট ধর্ম, আর লুক্রিশাস ও তাঁর গুরুরা পেগানদের সঙ্গে এক কোনায় দাঁড়িয়ে রইলেন প্রায় দু’হাজার বছর। যাই হোক, ১৬শ ও ১৭শ শতকে ফের জেগে ওঠে এপিকিউরীয় চিন্তা-ভাবনা। ১৮শ শতকে আসে আলোকপ্রাপ্তি (Enlightenment) ও নতুন বিজ্ঞানের যুগ, যা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ ক’রে এপিকিউরীয়দের ধ্যান-ধারণার প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। উনবিংশ শতকে এপিকিউরিয়াস ও লুক্রিশাসের মৌলিক চিন্তাধারাগুলো পাশ্চাত্য জগতের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাপদ্ধতির একটির মধ্যে সন্নিবেশিত হয়, আর তা হলো বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ, যেটার নাম-ই বলে দেয় সেটার প্রেরণার উৎস কোথায়। কার্ল মার্ক্স তাঁর পিএইচডি গবেষণা সন্দর্ভ লিখলেন এপিকিউরাসের ওপর, এবং এই দুই চিন্তাবিদেরই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট সাজুয্য ছিল, বিশেষ করে তাঁদের এই দৃঢ় বিশ্বাসে যে মানুষের কাঁধ থেকে ধর্মের জোয়াল সরিয়ে নিয়ে তাদের প্রভূত উন্নতি করা যায়। আজ মার্ক্স ঠিক লুক্রিশাস চিরকাল যেমন ছিলেন তেমনই অপঠিত, কিন্তু তাঁর আর তাঁর সমমনাদের ধ্যান-ধারণা এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাধারাকে এমন প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে যে এক সময়ে তা বিতর্কিত ও নতুন বলে মনে হলেও আজ সেটাকে তুচ্ছ ও দিবালোকের মতো স্পষ্ট বলে মনে হয়।
Marcus Tullius Cicero, যাঁকে আমরা মূলত একজন অসাধারণ বাগ্মী এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে চিনি, তিনিও বেশ কিছু দার্শনিক রচনা লিখে গেছেন। তিনি অবশ্য দাবি করেননি যে সেখানে তিনি মৌলিক কোনো চিন্তার কথা বলেছেন, কিন্তু গ্রীকদের ধ্যান-ধারণাকে একটি যথার্থ সাহিত্যিক আঙ্গিকে লাতিন ভাষায় উপস্থাপন করাকে তিনি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। আর সেই উদ্দ্যেশ্যে তিনি কিছু কাল্পনিক সংলাপ রচনা করেন যেখানে তিনি নিজে (সিসেরো) আর তাঁর কয়েকজন বন্ধু প্রায়ই মুখ্য চরিত্রে হাজির। আলোচিত বিষয়গুলো হচ্ছে মৃত্যু, আর মৃত্যু-পরবর্তী জীবন, কর্তব্য, শুভ-অশুভ, বন্ধুত্ব ও বৃদ্ধকাল। এবং এসব বিষয়ের আলোচনায় যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনার চাইতে জোর দেয়া হয়েছে জীবন সম্পর্কে একটি নির্দেশনার ওপর। আর মতামতগুলোকে একে অপরের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে, যদিও সিসেরো নিজে সরাসরি কোনো পক্ষ নেননি। কিন্তু ভদ্রলোক লিখেছেন বড্ড অবাক করা গতিতে; বেশির ভাগ রচনাই এক বছর সময়ের মধ্যে লেখা, যে সময়টায় সিসেরোর হাতে খুব একটা কাজ ছিল না। আজও সে লেখাগুলো অনায়াসে পড়া যায়, বিশেষ করে কারো নিজস্ব চিন্তাভাবনার প্রারম্ভিক পর্যায় হিসেবে।
লেখক সেনেকার জীবন কাল সিসেরোর একশ বছর পর, এবং প্রথমত, দার্শনিক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন তিনি। সিসেরোর মতো তাঁরও যথেষ্ট নাম-ডাক ছিল রোমক সমাজে। গৃহশিক্ষক ছিলেন তিনি নিরোর, যিনি খুব কম বয়েসেই সম্রাট হন। সেনেকা এবং আরেক ভদ্রলোক সম্রাটের অভিভাবক হিসেবে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। সে যা-ই হোক, কয়েক বছর পর সম্রাটের বিরাগভাজন হন তিনি এবং তাঁকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়। বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেনেকা বৈরাগ্যদর্শনের গুণ-গান গেয়ে, এবং এই দর্শনের ধারণাটি তিনি নিয়েছিলেন তাঁর গ্রীক পূর্বসূরীদের কাছ থেকে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে রয়েছে যার যার কর্তব্য করে যাওয়া (গীতার ‘মা ফলেষু কদাচন’?), সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত সহায়-সম্পদ ব্যবহার করা, ধন-সম্পত্তি এবং জাগতিক লাভালাভের প্রতি বিতৃষ্ণা, শাশ্বত জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, এবং পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা।
এই ধ্যান-ধারণাগুলো খৃষ্টধর্মের শিক্ষার সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। সত্যি বলতে কি, এমন একটা গুঞ্জন উঠেছিল যে সেনেকা আসলে খৃষ্টান-ই, বা অন্তত খৃষ্টানদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ আছে তাঁর। এমনকি, তাঁর ও বাণী-প্রচারক বা এপসল পঅলের মধ্যে জাল পত্র-বিনিময়েরও অস্তিত্ব রয়েছে। কাল অনুযায়ী বেশ খাপে খাপে মিলে যায়, যেহেতু সেনেকার মৃত্যু ৬৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে, আর পঅলের, খুব দেরি হলে, ৬৭ তে। ইউরোপের ইতিহাসের একটি দীর্ঘ সময় জুড়ে সেনেকার দর্শন খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে এসেছিল, যার একটি বড় কারণ নিশ্চয়ই এই যে সে-দর্শনের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের বড্ড মিল। সে যাই হোক, সেনেকার অনুরাগী বলতে তেমন কেউ ছিলেন না, কারণ তাঁর দর্শন বা শিক্ষা আর তাঁর কাজের মধ্যে মিল ছিল না বড় একটা। অর্থ-সম্পদ ঘৃণা করার কথা মুখে বললে কি হবে, তিনি নিজে কিন্তু বেশ ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন সব কিছুই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করবেন, কিন্তু বাস্তব জীবনে তাঁর আচরণকে ঠিক বীরোচিত বলা যায় না।
কথা ও কাজের এই অসংগতিকে কিভাবে বিচার করবো আমরা সেটা নিয়ে বিতর্ক আছে, কিন্তু সে বিষয়ে কারো সিদ্ধান্ত যা-ই হোক না কেন প্রাচীনকালের সবচাইতে বিখ্যাত দুই রোমক দার্শনিক সিসেরো এবং সেনেকা যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নেতৃত্বদানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন সেটি আমাদের জন্য একটি আকর্ষণীয় ব্যাপার। দুজনেই অন্যান্য সাহিত্যিক রচনাও সৃষ্টি করেছেন, এবং কম বয়েসেই বাগ্মী হিসেবে নিজেদের পেশাগত অবস্থান তৈরি করেছেন। এ-থেকে খানিকটা ধারণা পাওয়া যায় রোমক সমাজে দর্শন ও সাহিত্যের অবস্থান কি ছিল। এক দিকে এই-দুই বিষয়ের ছিল অসাধারণ মর্যাদা, এবং লেখকেরা রাষ্ট্রে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা রাখতেন। অন্যদিকে, সেগুলো ছিল অবসর বিনোদনেরও উপায়। তবে জীবনে প্রকৃত সাফল্য অর্জন করতে দার্শনিক বা কবি বা ঐতিহাসিক হলে কিন্তু চলতো না, হতে হতো লোক-বক্তা।
. . .
বিদ্যালয় এবং কুইন্টিলিয়ান
যেহেতু রোমে সাফল্য অর্জন অনেকটাই নির্ভর করত জনসমক্ষে বক্তব্য রাখার ওপর, তাই এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে মা-বাবারা চাইতেন তাঁদের সন্তানেরা যেন চমৎকারভাবে কথা বলতে শেখে। রোমের স্কুলের পড়াশোনা বলতে মূলত এটাই বোঝাতো। প্রাচীন গ্রীসেও বাচ্চাদের জন্য বিদ্যালয় ও শিক্ষক ছিল, এবং রোমকরা সেখান থেকেই ধারণাটা পেয়েছিল। গোড়ার দিকে অবশ্য শহরের সম্পন্ন মানুষেরাই তাঁদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাত, যদিও খুবই ধনী মানুষেরা তাদের বাড়িতেই শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে পারত। ঠিক কত শিশু বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করত তা বলা মুশকিল, কিন্তু একথা সত্য যে, শহরের জনসংখ্যার একটা অংশ পড়তে জানতো, আর সম্ভবত বেশিরভাগ শহরেই বিদ্যালয় ছিল।
বিদ্যালয়ের প্রথম কয়েক বছর শিশুদেরকে পড়তে, লিখতে আর খানিকটা পাটীগণিত শেখানো হতো, অনেকটা আজকের দিনের মতোই। শিক্ষার মাধ্যম ছিল অবশ্যই লাতিন। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর দৌড়-ই ছিল সম্ভবত ওইটুকুই। যারা ওই গণ্ডী ছাড়িয়ে আরো এগিয়ে যেতে চাইত, তাদেরকে একটা বিদেশী ভাষা — গ্রীক — শিখতে হতো, এবং লোক-বক্তৃতাতে প্রশিক্ষণ নেয়া শুরু করতে হতো। সেই প্রশিক্ষণে থাকত, অংশত, আগে থেকে জানিয়ে দেয়া বিষয়ের ওপর শিশুদের বক্তৃতা। এধরনের বক্তৃতাকে বলে ‘declamationes’ ‘নির্ধারিত বক্তৃতা’ (declemationes)। বাগ্মিতার তত্ত্ব-ও শিখতে হতো তাদের, যা নিয়ে আগেই কথা বলেছি আমরা, আর তাতে থাকত যুক্তি খোঁজা, মুখস্ত করা, ইত্যকার নানা কলা-কৌশল। কি করে তা করা হতো সে সম্পর্কে অনেকটাই জানতে পারি আমরা কুইন্টিলিয়ানের লেখা বারো খণ্ড বা পর্বের বা বইয়ের এক বিরাট নির্দেশিকা ‘Institutio oratória’ বা, ‘বাগ্মিতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ’, বা, আরো সহজভাবে বললে, ‘লোক-বক্তৃতার নির্দেশিনা পুস্তিকা’ থেকে। এটাতে লেখা আছে লোক-বক্তার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক নানান কথাবার্তা; শৈশব থকে সাবালকত্ব পর্যন্ত সময়ের সব কিছুই বর্ণনা করা আছে এতে। রোমের শিক্ষার একটা সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় এই বইটি থেকে।
বিশেষ করে, জানা যায় লোক-বক্তা হওয়ার লক্ষ্যটাকে কি করে অন্য আর সমস্ত শিক্ষাসংক্রান্ত বিবেচনাকে ছাপিয়ে যেতে দেয়া হলো সেই কথাটা। কুইন্টিলিয়ান নিঃসন্দেহে বেশ সংবেদনশীল আর চতুর মানুষ ছিলেন, যিনি একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গী আর বিচিত্র রকমের দক্ষতা অর্জনের ওপর জোর দেন, কিন্তু লক্ষ্যটা আগাগোড়াই খুব স্পষ্ট। জরুরি বিষয় হলো শিক্ষার্থীকে একজন সফল বক্তা হিসেবে গড়ে তোলা। আর এই দৃষ্টিভঙ্গীর একটি ফল দাঁড়িয়েছিল যে লাতিন ভাষাটি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল বিদ্যালয়ে। ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান বক্তার একটি প্রাথমিক হাতিয়ার; এছাড়া একটি মৌলিক চাহিদা ছিল এই যে শিক্ষার্থীরা শুদ্ধভাবে কথা বলতে শিখবে। কাজেই, গোড়া থেকেই ব্যাকরণ আর ভাষাগত শুদ্ধতা অত্যন্ত গুরুত্ব পেতো। এরপর এলো বিভিন্ন স্তরের শৈলীগত অনুশীলন, সাদামাটা দৈনন্দিন জীবনের ভাষা থেকে শুরু করে বিশদ বর্ণনা হয়ে আবেগের প্রবল বিস্ফোরণ অব্দি। লোক-বক্তাকে তার ভাষার সম্পদ সম্পর্কে প্রতিটি স্তরেই সচেতন থাকতে হতো, এবং সম্ভাব্য সেরা উপায়ে তা ব্যবহার করতে সক্ষম হতে হতো। তো, বিদ্যালয়ের এমন পড়াশোনার পর এটা নিশ্চয়ই মোটেই অবাক করা ব্যাপার নয় যে সেরা রোমক লেখকদেরকে শৈলীগত দিক থেকে কখনোই টেক্কা দেয়া যায় নি। চমৎকার করে কথা বলতে পারা, আর দরকার হলে, চমতকার লিখতে পারাটা ছিল শিক্ষার সর্বোচ্চ লক্ষ্য।
অবশ্য অপর দিকে তার অর্থ বিদ্যালয়গুলোতে অন্য ধরনের জ্ঞানের দিকে নজর দেয়া হতো না। ছাত্রী-ছাত্রদের নিশ্চয়ই অনেক কিছু পড়তে হতো, বিশেষ করে লাতিন আর গ্রীক ভাষার সেরা লেখকদের রচনা; কিন্তু তাঁরা কি লিখেছেন সেটা আবিষ্কার করা নয়, বরং তাঁদের ভাষা ও শৈলী পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণ করাই থাকত সেই পাঠের মূল উদ্দেশ্য। সব ধরনের সাহিত্যকেই দেখা হতো বক্তৃতা সংক্রান্ত অনুশীলনের উপাদান হিসেবে। এভাবেই শিক্ষার্থীদের পড়া হয়ে যেত ইতিহাস ও দর্শনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ, তবে জ্ঞানরাজ্যের অন্যান্য শাখার কোনো প্রবেশাধিকার সেখানে ছিল না বললেই চলে। প্রাথমিক পাটীগণিতের পর গণিতশাস্ত্র চর্চায় ছেদ পড়ত, এবং পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহীদেরকে তাদের শখ পূরণ করতে হতো বিদ্যালয়ের বাইরে। প্রযুক্তি, অর্থনীতি, এবং চিকিৎসাশস্ত্রের কোনো ঠাঁই ছিল না রোমক শিক্ষাব্যবস্থায়।
তো, এরকম শিক্ষা ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে যে বিতর্ক হবে তা অনুমান করা বিচিত্র কিছু নয়। তা যে কিছু হতো না তা-ও নয়, কিন্তু পাঠ্যক্রমের বিষয় কি হবে না হবে তা নিয়ে তর্কটা না হয়ে সেটা এই সমালোচনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো যে সেযুগে বাগ্মিতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ছিল অতি মাত্রায় তত্ত্বগত ও অবাস্তব। এই বিতর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন সেনেকা, যিনি ছিলেন, আমরা আগেই বলেছি, অত্যন্ত সুপরিচিত একজন লোক-বক্তা। এক পর্যায়ে তিনি লিখলেন, ‘Non vitae sed scholae discimus’, মানে, ‘আমরা জীবনের জন্য শিখি না, বিদ্যালয়ের জন্য শিখি’, যে-কথা দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন শ্রেণীকক্ষের অনুশীলন শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণীকক্ষের অনুশীলনের চাইতে ভালো কিছু হওয়ার শিক্ষা দেয় না। কিছুদিনের মধ্যেই এই কথাটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে এক অনস্বীকার্য সত্যে রূপ দেয়া হলো : ‘Non scholae sed vitae discimus’, মানে, ‘আমরা বিদ্যালয়ের জন্য শিখি না, জীবনের জন্য শিখি।’ মোটের ওপর কথাটা সত্য কিনা তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, তবে সেনেকা যে একথা বোঝাতে চাননি সেটা নিশ্চিত।
(ক্রমশ)
Have your say
You must be logged in to post a comment.
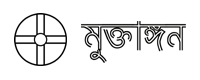
২ comments
Pingback: লাতিন ভাষার কথা : ১৭ | জি এইচ হাবীব
Pingback: লাতিন ভাষার কথা : ১৮ » বাংলাদেশী শীর্ষ কমিউনিটি নিউজ পোর্টাল