১
আমার পিসিদের তিনজনকে আমি ছোটবেলা থেকে আমি মা বলতে শিখেছি — রাঙামা, ফুলমা, ছুটুমা। সম্ভবত, তাঁদের জৈবিক অর্থে কোনো সন্তান ছিল না বলে, অন্য পিসিরা এবং আমার মাবাবা এই শিক্ষাটা দিয়েছিলেন।
মার মতোই আমার পিসিরা, সবাই। মমতায় কাছে টেনেছিলেন তাই নয়, মানুষও করেছিলেন। যে যেভাবে পেরেছেন। প্রত্যেকের হাতেই দেয়ার মতো অজস্র সম্পদ ছিল যে!
শেষের জন, মুক্তি মজুমদারের সান্নিধ্যে এসেছি অনেক ছোটবেলা থেকেই, তবে প্রবাস থেকে ফেরার পর সাড়ে দশ বছরের আমি থেকে পরিণত বয়েসি আমি পর্যন্ত আমার প্রত্যেক দিনই ইনি আমার চেতনার অংশীদার হয়ে রয়েছেন। ভালোবাসায়।
২
আসলে ছুটুমাই বোধ হয় আমাকে রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন চিনিয়েছেন, আর চিনিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের গান, নতুন করে, নতুন আঙ্গিকে। আমার যৌবনকে করেছেন টালমাটাল, অপূর্ব।
শান্তিনিকেতনের পরিবেশের আভা তাঁর জীবনে, তাঁর ব্যক্তিত্বে; এটা তাঁর খোলস নয়, তাঁর ধাতু। আবার বাংলাদেশের সচেতন, সাহসী, অসাম্প্রদায়িক পরিবেশের পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর সুবাস। আমি ওই সুবাসে আসক্ত হয়েছিলাম ছোটবেলায়, তাই ছুটুমার বাড়ি যেতে চাইতাম সুযোগ পেলেই।
গেলেই বাবার আনা লংপ্লেতে ভারতীয় রাগসঙ্গীত, অথবা চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, অথবা নানা রঙের স্বাদের পুরনো রেকর্ড আমাকে শুনতে দিতেন। আমি সেই সব গান মন্ত্রের মতো বসে বসে শুনেছি, জয়নুল আবেদিন অথবা নন্দলাল বসুর স্কেচের বই হাতড়েছি। অদূরে ধানক্ষেত তখন সবুজ আভায় টুসটুস করছে। ‘আমার যায় বেলা বয়ে যায় বেলা কেমন বিনা কারণে’, শুনতে শুনতে সময় থমকে থেকেছে। সেসব দিনে ছুটুমার গলায় শুনেছি মায়াবী ব্যঞ্জনার গান, নিভৃতে, সেই গ্রামীণ বাংলাদেশের নির্জন, নিরালা সুস্বাদু পরিবেশে, ‘কী সুর বাজে আমার প্রাণে, আমিই জানি, মনই জানে’। উনি জেনেছেন, আমিও বোধ হয় জেনেছি তখন, সেই ছোটবেলাতেই।
কেউ বাধা দেয়নি। বরং ছুটুমার কাছে গান শিখতে আসা প্রাণের মেলায় মিলতে আসা শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীদের ভিড়ে আমিও মিশে গিয়েছি, শিখেছি এমন সব গান যা আমি আগে শুনিনি, ‘মোরা সত্যের ‘পরে মন আজি করিব সমর্পণ’ অথবা ‘জাগো নির্মল নেত্রে রাত্রির পরপারে, জাগো অন্তরক্ষেত্রে মুক্তির অধিকারে’ — প্রবাসে চার বছর কাটিয়ে আসার পর গান, বাংলা ভাষা আর সুমধুর পরিবেশের এই বন্যা, আমার কৈশোরকে, যৌবনকে কোনো বিশাল স্বপ্নকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করেছে।
এর একটা কারণ বোধ হয় আমার জীবনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে, অর্থাৎ আমার প্রাক-বয়ঃসন্ধির সময় থেকে শুরু করে যৌবন পর্যন্ত, ছুটুমা আমার কাছে ছিলেন, অনেকটা কাছে, যাওয়া-আসা ছিল খুব নিয়মিত। উনিও প্রায়ই চলে আসতেন রাজশাহীতে।
৩
আমার সোনাপিসে মোহাম্মদ কায়কোবাদ। এদের দুজনের কমরেডের মতো ব্যবহার। ‘শেষের কবিতা’র অমিত আর লাবণ্যর মতো, এঁদের থাকার মধ্যে অঢেল অশেষ space — কোনো আরোপ নেই, নালিশ নেই, দুজনের দুটি আলাদা ঘর, সোনাপিসে কখনো আমি বা আমরা গেলে সামনে এসে ওজন জাহির করতেন না, আড়ালে আড়ালে থাকতেন, যেন অম্লজান, আছেন, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। বটবৃক্ষের মতো, সারা জীবন বোধহয় সংসারটা এভাবে সামলেছেন উনি। সারা জীবন ছুটুমা রানীর চেয়েও দৃপ্ত মহিমায় রাজত্ব করেছেন তাঁর ভুবনে।
এঁদের এই নির্মল শান্তিময় নীড়, যা সহজেই বিশ্বজগতের আস্তানা ও আশ্রয় হয়ে উঠত বিকেলবেলায়, একে দেখে আমার একটু ভুল ধারণা হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম দাম্পত্য বোধ হয় এরকমই হয়। পারস্পরিক আস্থা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসার একটা এমন মিশেল যেখানে কথার বাহুল্য নেই, ঝগড়া বিবাদ নেই, স্বার্থ সংঘাত নেই, হিংসা নেই, নিরাপত্তাহীনতা নেই, যেখানে কাউকেই নিজেকে ছোট করে খাটো করে রাখতে হয় না । কিন্তু বাস্তবতা তো তেমন নয়! বাংলাদেশের, এমনকি পৃথিবীর মেয়েরা প্রায় বেশির ভাগ নিজের সম্পূর্ণ চেতনা উন্মীল করে, নিজেকে কাঁচি দিয়ে না কেটে, শাবল দিয়ে না মুড়িয়ে, মুখোশ না পরে, গলার স্বর না বদলে, বেঁচে থাকে না বিশ্ব-সংসারে। তাই ছুটুমার প্রায় নির্ভীক, উদাত্ত জীবন, কত যে আলাদা, কত যে অসাধারণ, তা আমি বুঝতে পারিনি ছোটবেলায়।
৪
ছুটুমা খুব ভালো গান করতেন, অনেকে সুচিত্রা মিত্রের সঙ্গে তাঁর মিল দেখতে পেত। আমার কাছে ছুটুমার কণ্ঠ ওই জাতীয় বলিষ্ঠ বটে, কিন্তু স্বর ও গায়কী সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব, স্বকীয়।
হৃদয়ের সব চেয়ে গহন প্রকোষ্ঠে যে বোধ থাকে, সেখান থেকে, অপরূপ সংবেদনের সঙ্গে, অসাধারণ উচ্চারণের সঙ্গে, নির্ভুল কথা ও জ্ঞানের সঙ্গে বেরিয়ে আসা।
পঞ্চাশোর্ধ্ব ছুটুমা বেতারে গান গাইতেন না আর, পাবলিক অনুষ্ঠানে গান গাওয়া ছেড়েছেন আগেই, যদিও শুনেছি, ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন, বাংলাদেশের শিল্পীদের নিয়ে কলকাতার মহাজাতি সদনে একটি অনুষ্ঠান হয়, সে-অনুষ্ঠানে উনি গেয়েছেন তাঁর অবিসংবাদিত প্রিয় গান, ‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে’। নাহ, ওই গানের ওই মাধুর্য, ওই গাম্ভীর্য, গভীরতা, আমি আর শুনিনি, সুচিত্রার গলায়ও বোধ হয় নয়।
শুধু গান নয়, সে-যুগে সত্যিকার সাংস্কৃতিক, উচ্চশিক্ষিত পরিবার বলতে খুলনার সুবোধ মজুমদার, তাঁর বাবা শরৎ মজুমদার এঁদের কথা কে না জানত।
শরৎ মজুমদার ছিলেন সেকালের রয়াল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটির ফেলো। ১৯০৭ সালে পদার্থবিদ হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশ বসু ও প্রফুল্ল রায়ের ছাত্র, পরে তাঁদেরই সহকর্মী। কটকে, তারপরে পাটনা কলেজের প্রিন্সিপাল।
সুবোধ ছিলেন কৃতী উকিল, পরে গণিতবিদ, তাঁর নামে খুলনার ব্রজলাল কলেজের ছাত্রাবাস এখনো আছে। ডাকসাইটে সাহসী লোক ছিলেন, গায়ে যেমনি জোর, তেমনি শিক্ষা, তেমনি প্রতিভা, তেমনি সাহস। প্রফুল্ল রায় চৌধুরী (নীলিমা ইব্রাহিমের বাবা) সুবোধকে তুলে ধরেছিলেন খুলনার সাংস্কৃতিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার প্রাণপুরুষ হিসেবে। তাঁর গুণের কথা শুনে তাঁকে বি. এল. কলেজে গণিতের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেয়ার অনুরোধ করা হয়।
সুবোধ একাধারে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ জানা মানুষ। বেহালা, সেতার, বীণা, পাখোয়াজ, তবলা, হারমোনিয়াম, বাঁশি, এস্রাজ জানতেন, কলকাতার সঙ্গীত একাডেমিতে গিয়ে তালিম নিয়েছিলেন, সেইসব আবার শিখেছিলেন তাঁর ছেলেমেয়েরা।
৫
যে দেশে সাম্প্রদায়িক মূর্খামি চূড়ান্ত, সেখানে সারস্বত সম্পদই প্রথম আক্রান্ত হয়, পাকিস্তান যুগে বিভিন্ন রায়টে ও সবশেষে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের সেই গ্রন্থাগার ও বাদ্যযন্ত্রগুলি ভেঙে পুড়িয়ে ফেলা হয়।
১৯৭০ সালে মারা যান তিনি, নাহলে আমার অসাধারণ সাহসী দাদামশাই সুধীর ঘোষের মতোই, তিনিও যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাক-সেনার হাতে নিহত হতেন, শহীদ হতেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।
তো, সেই পরিবারের মেয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনচেতা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হবেন, সেটা স্বাভাবিক — এ নিয়ে সোনাপিসেও হালকা ঠাট্টা করতেন।
প্রত্যেকে নিজের মতে খুব শক্ত ছিলেন। ছুটুমা বিশেষ করে এমন যুক্তি দিয়ে কথা বলতেন যে কুসংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাস অথবা নিছক মূর্খ মৌলবাদী অবস্থান থেকে যাঁরা কিছু কথা তুলে আসত, তারা বেশ বেগতিকে পড়ত।
এক-একটি যুক্তি দিয়ে উনি এদেশের সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার, কুশিক্ষা, ফালি ফালি করে দিতেন। এভাবে কত জনকে জাগিয়েছেন, মানুষ করেছেন, তার কোনো গোনাগুনতি নেই। বলতেন, আমি এটাই পারি, এটাই আমার মিশন, দেশের জন্য।
আমি ওঁর অনেক সহযোদ্ধাদের বলতে শুনেছি, মুক্তি মজুমদারের মতো দশটা মানুষ বাংলাদেশে থাকলে দেশটা বদলে যেত।
স্বার্থবাদী ছিলেন না বলে বোধ হয়, কোনো দিন তাঁর সরকারি চাকরির সুবাদে তাঁকে কোনো ফন্দিতে কেউ বদলি করতে পারেনি।
একবার এক দল ছাত্র শিবিরের গুণ্ডা তাঁর পিছু নিয়েছিল তাঁর কলেজেই, কিন্তু তাঁর ছাত্ররা আগেই খবর পেয়ে তাঁর অজান্তেই তাঁকে ঘিরে ফেলে। এমন দাপট নিয়ে থাকতেন। অমন সৎ-সাহস কম লোকের দেখেছি, ‘হিন্দু নামগন্ধী’ মানুষের তো কমই দেখেছি বাংলাদেশে (সেটা তাঁদের লজ্জা নয়)।
৬
সত্তর, আশির দশক জুড়ে ও নব্বইয়ের দশকের শেষের দিক পর্যন্ত ছুটুমা ও সোনাপিসে তাঁদের কর্মক্ষেত্রে ও খুলনার মূলধারা সাংস্কৃতিক জগতে, অসাম্প্রদায়িক আন্দোলনে, মুক্তশিক্ষার আন্দোলনে পুরোধা ছিলেন। সে-সব কথা তাঁর সহযোদ্ধারা আরো ভালো বলতে পারবেন।
ছুটুমাকে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের নেতৃত্ব দিতে দেখেছি। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিদেব ঘোষদের আমন্ত্রণ করে আনেন তাঁরা এসময়, বলা বাহুল্য উপযুক্ত সহকর্মী ও বিশ্বস্ত বন্ধুরাও ছিলেন পাশে। শুনেছি হাদিস পার্কের খোলা মঞ্চে গভীর রাতে কণিকার ‘বিরহ মধুর হলো আজি’ শুনে, অথবা শান্তিদেবের শুভ্রতা দেখে ও বাউল গলা শুনে, অনেক রিক্সাওয়ালা ও সাধারণ মানুষ মনে করেছিল এরা সব ‘আল্লাহ-ওয়ালা’ মানুষ, চোখে জল ছিল তাঁদের। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এমন মাঠেঘাটে প্রত্যন্তে চলে গেছিলেন এঁরা।
যারা বলে রবীন্দ্রনাথ এলিটদের ড্রয়িংরুমের জন্য, সমঝদারদের জন্য, তারা ভুল বলে। এটা আমার হাতে-কলমের শিক্ষা। পরে আমরাও দীর্ঘ কয়েক বছর সংগঠন করেছি, ভুলভাল যাই করি না কেন, তার আদর্শের ছবিটা এখান থেকেই পেয়েছি।
রবীন্দ্রসঙ্গীতকে হয়ে উঠতে দেখেছি অসাম্প্রদায়িক, মুক্ত, সুন্দর সমাজ গড়ার হাতিয়ার। হাতিয়ার, কারণ এই সব কাজ বড় পরিধিতে করতে গেলে, সমাজকর্মীই হতে হয় — সাংস্কৃতিক কর্মীরা তো তা-ই।
৭
গান — রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে ছুটুমার প্রথম দিকের পাঠগুলি মনে পড়ে। মুখ বিকৃত হচ্ছে কিনা, দুলে দুলে গাইছি কিনা, শিরদাঁড়া সোজা কিনা, কত কিছু তীক্ষ্ণচোখে দেখতেন। তখন উঠতি বয়েস, একটু ভয় পেতাম বৈকি। পরে বুঝেছি গান গাইবার সময় বসার আসন ও দেহভঙ্গির মধ্যেই ধ্যানের একটা ভাব ফুটে উঠছে কিনা, গান পূর্ণ মর্যাদা পাচ্ছে কিনা, নাকি গান-বহির্ভূত কোনো চাপল্য বা অমনোযোগিতা ঢুকে পড়ছে, সেগুলি খেয়াল রাখতেন, এবং তা শুধু আমার জন্য প্রযোজ্য ছিল এমন নয়।
গান একটা প্রবল বন্যার বেগের মতো কর্ণকুহরে ও অন্তরে প্রবেশ করছে সে সময় (১৯৮৬-১৯৯৯), রাজশাহীতে আমাদের বাড়িতে, আমার পিসিদের সূত্রে, ছুটুমা সোনাপিসের খালিশপুরের বাড়ি ‘কল্যাণী’ এবং রাজশাহী ক্যাম্পাসের গানের ঐশ্বর্যময় পরিবেশ থেকে। সে নিমগ্নতায় নতুন গান শিখেছি অনেক, ভালোবেসেছি রবীন্দ্রনাথকে ক্রমশই।
ছুটুমার কাছে উপহার পেয়েছি অজস্র, আর বই পেয়েছি বেহিসেবি ভাবে। যে কোনো ভালো বই আমার জন্য রেখে দিতেন (শুধু আমার জন্য নয় বোধ হয়, এমন অনেক স্নেহের পাত্রপাত্রী তো তাঁর সর্বত্র ছিল)। এগুলির মধ্যে বিশেষ দাগকাটা কয়েটি বই ছিল সুকান্ত-সমগ্র, শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সমগ্র।
আমার কলেজ জীবনের আগেই ‘শান্তিনিকেতন’ — রবীন্দ্রনাথের দুটি বই আমাকে দেন, দেন ‘পুনশ্চ’, ‘পত্রপুট’, আনকোরা নতুন ‘গীতবিতান’ (বাড়িতে তো ছিলই, এগুলো একান্তভাবে আমার উপহার)। ছুটুমার সেই গীতবিতান আমার কলেজ জীবনের পাঁচ বছর, তারপর আরো উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়া যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচ বছর, আমার হাতে হাতে ঘুরত।
যে-কোনো গান না শুনে থাকলে আমি বরাবরই বাবা অথবা ছুটুমার শরণাপন্ন হয়েছি। আজও দেখি মারাত্মক বিপর্যস্ত শরীরে তিনি যতই খুঁটিনাটি সাধারণ জিনিস ভুলে যান, গানের কথা, সুর, কদাপি ভোলেন না।
গান যে গেয়ে যেতে হবে, নিজেই গান নির্বাচন করতে হবে, গানের কথা ভুলে যাওয়া মানে আসলে গানের প্রতি অবিচার, অবিমৃষ্যকারিতা, সে-সব ছুটুমাই তো একদম ছোট থেকে শিখিয়েছেন। আমাকে শুধু নয়, অন্যদেরও বলতেন, আমরা পাঠ নিতাম। গান গাইবার সময় কী কী নিয়ে হাজির হতে হবে, অর্থাৎ খোল, তবলা, হারমোনিয়াম, গীতবিতান দুই খণ্ড, এবং হয়ে গেলে আবার সেগুলি যথাস্থানে রেখে আসার নিয়ম, এগুলোও ছুটুমা শেখাতেন। সরকারি চাকরি থেকে দুজন অবসর নেবার পর গ্রামে গিয়ে ছোট ছোট শিশুদেরও এভাবে তৈরি করেছিলেন।
আমাদের যাদের গলায় সুর নেই, গায়কী নেই, তাল নেই, তাদেরও রবি ঠাকুরের গান শুধু শুনতে নয়, গাইতেও প্রেরণা দিতেন। বলতেন, গান গাইবি, দেখবি সব বিপদ জয় করতে পারবি।
ছুটুমা তো গণজাগরণের জন্য, হৃদয়ের মুক্তির জন্য, গানকে গ্রহণ করেছিলেন, তাই সেখানে উত্তম-অধম ছিল না, প্রতিযোগিতা ছিল না, আনাড়ি-সমঝদার-এর শ্রেণিভেদ ছিল না, আত্মসচেতনতা ছিল না, ছিল পাখির মতো গান গাওয়া, সকাল-সন্ধে বেলায়, শোকে মৃত্যুতে, অন্ধকারে, আলোয়।
৮
লিখতে গিয়ে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে যাওয়া দোষের হয়তো! আশা করি, এইসব ঘটনা থেকেই একটা সামগ্রিক ছবি কিছুটা হলেও পাওয়া যাবে। অস্বস্তি, ঘটনাগুলো আমার জীবনের, এটি সামান্য ব্যক্তিগত স্মরণ ও বিশ্লেষণ; ঘটনার সারিসারি সাজানো তথ্যপঞ্জি নয়।
সাড়ে পাঁচ বছরে আফ্রিকা চলে যাওয়া, ও সেখানে ইংরিজি মাধ্যমে পড়াশুনো করার পর, সাড়ে দশ বছরে যখন দেশে ফিরলাম, ছুটুমা আমাকে বাংলা থেকে দূরে সরে গেছি, বোধ করি এই চিন্তা থেকে অনুবাদ করতে দিলেন একটি বই, জওহরলাল নেহেরুর লেখা, ‘লেটার্স ফ্রম আ ফাদার টু হিজ ডটার’ — বাংলায় পরবর্তীকালে অনুবাদ চোখে পড়েছে বইটির; বহুল-পঠিত বই, ‘মা-মণিকে — বাবা’।
লেখাটি ইংরিজিতে পড়তে খুব প্রাঞ্জল; ত্রয়োদশী ইন্দিরাকে জেল থেকে লেখা ইতিহাস, বিবর্তন, সভ্যতা এসব নিয়ে। এক বাবা তাঁর কন্যাকে জেল থেকে কীভাবে পড়াশুনোর পাঠ দিচ্ছেন, বিষয়টি ভাবলেই তো ভালো লাগে। আমার বাবা, যিনি পড়াশুনো ও বিস্ময়কর আনন্দ-দানকে কখনো আলাদা করেননি, তাঁর কথাও যেন মনে পড়ে গেল। আর কী অসাধারণ প্রাঞ্জল গদ্য, দেখে বিস্ময় লেগেছিল।
লেখার খাতা ছিল বিস্তর। আফ্রিকায় থেকেও অনেক বাংলা লেখালেখি করতাম, আর যা বাংলা বই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাও খুব কম ছিল না।
নেহেরুর লেখার অনুবাদ, ওই প্রথম ‘সিরিয়াস’ লেখা, আর প্রথম বাংলা অনুবাদ তো বটেই। প্রবাস-ফেরত সাড়ে দশ বছরের শিশুকে একই সঙ্গে ক্লাস সেভেনে সোজা ঢুকে যাওয়ার জন্য কিছু বাংলায় লেখালেখির প্রস্তুতি (যদিও তা মুখ্য ছিল না), আত্মবিশ্বাস তৈরি, ইতিহাস-জ্ঞান, ও ভাষার প্রতি ভালোবাসা শেখানোর জন্য এর কোনো বিকল্প ছিল না বোধ হয়।
বাংলা অভিব্যক্তি, কবিতা, গদ্য, প্রবন্ধ, উচ্চারণ, বানান, বাগধারা, ইত্যাদি বিষয়গুলিতে চৌম্বকীয় আকর্ষণ ছিল ঠিকই, কিন্তু এর পেছনে একজন মানুষের হৃদয়ের উত্তাপ ছিল। সেই হৃদয়ের উত্তাপ ছাড়া পৃথিবীর কোনো ইতিবাচক, সৃষ্টিশীল কাজ সফল হয় না, যত ছোট পরিসরেই তা হোক না কেন। একটি শিশুকে এতখানি সময় ও উত্তাপ দিতে পারেন শুধু মা-বাবা, এ কথা সত্য নয়। ব্যক্তিগতভাবে শিখেছি, এই উত্তাপ যে-কোনো হৃদয় থেকে আসতে পারে।
পরবর্তী সময়ে কী কী বই পড়তে পারি, তার পরিচয়টা অনেকটাই পেয়েছিলাম ছুটুমার কাছ থেকেই। লেখালেখির মূল উৎসাহ ছুটুমা দিয়েছিলেন আগাগোড়াই, এমনকি তেরো বছর থেকে শুরু করে প্রায় তেইশ বছর পর্যন্ত লেখা কবিতার ক্ষেত্রেও। যে-কোনো ইতিবাচক, শিল্পময়, সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহ দেবার লোক খুব বেশি তো আমরা পাই না।
সম্ভবত প্রাক্তন প্রবাসী শিশুর বাংলা চর্চাকে উস্কে দেবার জন্য ছুটুমার একটা মমতা কাজ করে যেত, অথবা কে জানে, হয়তো নিজের শৈশবের সেই টানটান সাহিত্য-চর্চার দিনগুলি তাঁর মনে পড়ে থাকবে। ছুটুমা যে নিজে ছোটবেলায় গল্প লিখতেন, হাতে-লেখা সাহিত্য-পত্রিকা বের করতেন ওঁরা ভাইবোনে মিলে, সে-সব পরে শুনেছিলাম।
অবশ্য এমন নিবিড় জীবনপাঠ আমার একারই অভিজ্ঞতা, তা নয় মোটেই। এমন অভিজ্ঞতা যে বেশ অনেক জনেরই, নানা বয়েস, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান, পারিপার্শ্বিকতার মানুষের হয়েছিল, কখনো গানের ক্ষেত্রে, কখনো লেখার ক্ষেত্রে, কখনো পড়ার ক্ষেত্রে, কখনো আদর্শগত ক্ষেত্রে, কখনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক্ষেত্রে, কখনো সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে — আর সে সংখ্যা ঠিক গুনে ফেলা যাবে না।
৯
পরবর্তীকালে আরো ভালো করে লক্ষ করেছি ওঁদের দুজনের প্যাশনকে, বইয়ের ভালোবাসাকে, আরেকটু নিবিড় ভাবেই। বাড়ির গ্রন্থাগার নেহাত ছোট ছিল না তাঁদের, আর ছুটুমা বলতেন দুই বাংলা থেকেই বিদ্বদ্জনেরা তাঁদের বই ও নানা মাপের, আকারের, বিষয়ের পত্রিকা পাঠান, কারণ হিসেবে ঠাট্টা করে বলতেন ‘সবাই জানে এঁরা গরীব শিক্ষক, তাই বই এমনি এমনি দিয়ে দেয়’। আমার এখান থেকে বাছাই প্রবন্ধ, লেখা, কবিতা, পড়ার সুযোগ হত। কতটা যোগাযোগ ছিল দুই বাংলা মিলে , ব্যাপারটা বিস্ময়কর। আর এখানে তাঁদের প্রাক্তন ছাত্র, বন্ধু বা স্নেহ ও শ্রদ্ধাভাজনদের অবদান কম ছিল না।
অল্প দামের বুকশেল্ফ, কিন্তু পড়ার ঘরটিতে একটা শুচিময়তা ছিল, আমার কাছে ওটাই শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, যত্নের দিক থেকে, উপাসনালয়। ও ঘরেই থাকত — খোল, ডুগি তবলা, হারমোনিয়াম, বেহালা আর মন্দিরা। ওখান থেকেই দেখা যেত বাড়ির বাইরের ছোট বারন্দা দিয়ে ধানক্ষেতের সবুজ পরিপূর্ণতা। এ সব খালিশপুরের তাঁদের কল্যাণীর বাড়িতেই।
সকালে গেলেও দেখা যেত, ছাত্রছাত্রীরা আছেন, তাঁরা অনেকে পাঠ নিতে আসতেন, কেউ আসতেন ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য, কেউ এমনিতেই, আত্মার আশ্রয়কে স্পর্শ করে যাবার জন্য, অন্তত আমার তাই তো মনে হয়েছে। অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী, যাঁরা বিপথে চলে যাচ্ছে, তাঁদের পড়াশুনোর দিকে ফিরিয়ে এনেছেন তাঁরা, জীবনের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। অনেকের চাকরির ব্যবস্থা করেছেন, অর্থিক সমস্যা মিটিয়েছেন এঁরা দুজন, পড়াশুনোর খরচ চালিয়ে গেছেন, এমন ঘটনাও আছে।
ব্যাপারটা এক-পাক্ষিক নয়; ‘গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়’, রবীন্দ্রনাথের ‘শেষের কবিতা’র লাবণ্যর লেখা সেই কবিতার বাক্যবন্ধ তো মোক্ষম। যাঁরা গ্রহণ করেছেন এই দান, তাঁরা ছুটুমা ও সোনাপিসেকে ভালোবাসার ঋণে ঋণগ্রস্ত করেছেন আরো, আর নিজেরাও তাই হয়েছেন। খালিশপুরের ‘কল্যাণী’ কল্যাণের একটি ছোটখাটো উৎসব ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে আমি যা-ই বলি, অন্যরা বাকিটুকু বলে, তথ্য পূরণ করে দেবেন, আশা করি।
১০
যতদিন ছুটুমা-সোনাপিসে খালিশপুরের বাড়িতে ছিলেন, ১৪ ডিসেম্বর সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ব্যানারে হাদিস পার্কে সারা রাত অনুষ্ঠান হত। এক রাত আমি ওই বাড়িতে ছিলাম, অনুষ্ঠান শেষে। এই রাত্রিদিন গুলি আমার জন্য রক্তের আখরে আঁকা। ছুটুমা বলতেন, ‘ওরা আসবে,’ — ‘ওরা দেখতে পাচ্ছে। তোর মনে হয় না?’
অন্ধকার রাতের দিকে তাকিয়ে সেই মুক্তিযুদ্ধের অসমসাহসী মানুষগুলিকে স্মরণ করে তাঁর চোখে জল দেখতে পেতাম।
সামনের সারিতে চেতনার লড়াই নিয়ে আছেন বলে প্রায়শ বলতেন ‘আমার ভয় নেই, ভরসাও নেই।’ কথাটি অন্যভাবে বুঝতে পেরেছি নিজের জীবনেও। ভয় নেই বলা সহজতর, ভরসা নেই, কথাটা আরো কঠিন।
জানি না, আমরা কেউই ভরসা ছাড়তে চাই কিনা, কিন্তু ছুটুমা বোধ হয় সম্পূর্ণ নিজের ওপর ভরসা করা ছাড়া আর কাউকেই ১০০ ভাগ টেকেন ফর গ্র্যান্টেড হিসেবে নিতে চাইতেন না।
‘পরিবর্তন একমাত্র নিয়ম’, এ কথাটি নিজেদের দিয়েও বুঝতে পারি শতভাগ। আজ চাইলেও তাঁর কাছে ছুটে যেতে না পারার সীমাবদ্ধতা পদে পদে ক্লিন্ন করে।
সমর সেন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান বা রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর কিছু মারাত্মক কবিতা তখন আমাদের সামনে দিনে-রাতে আবৃত্তি হচ্ছে। চলে যাচ্ছে মাঠেঘাটে।
এমনকি মাঠ ঘাট থেকে আসা ছাত্ররাই তো তাঁর আশেপাশে অনেকেই।
তাঁদের মধ্যে একজন মৃত্যুঞ্জয় হালদার। তাঁর কথা বলতে গেলে আজও হাত অবশ হয়ে আসে। এমন কেউ নেই তাঁকে ভালবাসত না, সমীহ করত না। আমি তো দূরের লোক, কাছের লোকরাও আজ পর্যন্ত সেই শোক, তাঁর অকালমৃত্যুর শোক ভুলতে পারেননি। মৃত্যুনদা কবিতা লিখতেন, অমন কবিতা আর হবে না।
মৃত্যুনদার দু-একটি ছবি — জলছবি, আমার কাছে ছিল। শরৎ-প্রভাতে একটি অসাধারণ কার্ডে নিজের হাতে ছবি এঁকে তাঁর অদ্বিতীয় হাতের লেখায় লিখে দিয়েছিলেন এই কবিতা: ‘নীল আকাশে মিঠে চাঁদ/ ঘাসের ওপর শিউলি ফাঁদ/ আনন্দ তোমায় আশীর্বাদ।’
ক্ষণজন্মা শিল্পী — আলপনা দিতেন; সত্যি, এমন আলপনা আমি আর কোথাও দেখিনি, কাউকে ছোটো না করেই বলা।
ভাস্কর্য বানাতেন। একজন ক্রীতদাসের ভাস্কর্য বানিয়েছিলেন, বাড়িতে এখনো আছে। মাটির ভাস্কর্য। অথচ মনে হয় পাথর কুঁদে তৈরি। চোখের দৃষ্টি, সেই হাতপা-বাঁধা মানুষটির, জানি না তাতে কী ছিল।
স্বশিক্ষিত, রামকিংকর বেইজের মতো। বেঁচে থাকলে এতদিন বড় শিল্পী হিসেবে নাম ডাক হত, বাংলাদেশের ইতিহাসে।
আর সেই শিল্পীকে অসীম দারিদ্র্য আর ধুয়ে-যাওয়া ভাগ্যরেখা থেকে উদ্ধার করেছিলেন ছুটুমারাই। অমন পরিশ্রমী ও প্রতিভাবান শিল্পী আর একই সঙ্গে অসমসাহসী যোদ্ধা আমি আমার চোখের সামনে আর দেখিনি । শিবির বিরোধী ভূমিকায় তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।
যখন আমি ক্লাস ইলেভেনে, তাঁর মৃত্যু হয় — আমাদের সম্মিলিত জীবন যেন ধসেই পড়েছিল সে সময়ে। তারপর থেকেই বোধ হয়, একটি অবিচ্ছিন্ন সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, যিনি স্বর্গে থাকেন ও সবার, বিশেষ করে মঙ্গলময়দের ওপর মঙ্গল বর্ষণ করেন, যিনি সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু, তেমন কোনো ঈশ্বরের ওপর আমার আস্থা চটে গেছে।
১১
সামনের গোড়ায় থাকত অনেক বই। ছুটুমার বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে প্রচুর বই ছিল। ১৪ ডিসেম্বর সারা রাত সাধারণ মানুষের মধ্যে হাদিস পার্কের খোলা মঞ্চে যে অনুষ্ঠান চলত তাতে গণসংগীত আর রবীন্দ্রনাথের গান থাকত। ‘কারা মোর ঘর ভেঙেছে স্মরণ আছে’, গানটি একটি ধারালো স্মৃতির মতো ঝাপটা দিত। ‘জনতার সংগ্রাম চলবে’… ‘মা গো ভাবনা কেন?’ গানটিতে অল্প পরিবর্তন করে করা হয়েছিল ‘আমরা প্রতিরোধ করতে জানি’!
একই সময় আমরা রাজশাহীতেও গানগুলি করছি।
রবীন্দ্রনাথের গান যে কীভাবে গণসংগীত হয়, তাও দেখতাম আমরা।
‘নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়’ বাংলাদেশের বিভিন্ন সময় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিস্মৃত ও অবলুপ্ত বা বিকৃত করার চেষ্টার সময় গাওয়া হয়েছে। ‘বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে।/ পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে’।
নতুন গানের মধ্যে শিখেছিলাম ওখানেই ওই সমস্ত অনুষ্ঠানের মহড়াতে, ‘রইলো বলে রাখলে করে, হুকুম তোমার ফলবে কবে/ তোমার টানাটানি টিকবে না ভাই, রবার যেটা সেটাই রবে।’ নন্দনে গানটি আমি শিখিয়েছিলাম। গালিব ভাই মজা করে বলতেন ‘রবার যেটা মুছবে সেটা’!
যা হোক, আরো বিবিধ গানের মধ্যে সেসময় শিখেছিলাম `আর নহে আর নয়, আমি করিনে আর ভয়’, ‘উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে ওই যে তিনি, ওই যে বাহির পথে’, ‘জাগো নির্মল নেত্রে, রাত্রির পরপারে, জাগো অন্তরক্ষেত্রে মুক্তির অধিকারে’, ‘মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব বিসর্জন, জয় জয় সত্যের জয়’ — এগুলি রাজশাহীতে শিখিয়েছিলাম। নন্দনে ও মুক্তিযুদ্ধ চর্চা কেন্দ্রে। পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উদীচী-তে।
এছাড়া নজরুলের গানও শিখছি আমরা ছুটুমার কাছে; রাজশাহীতে শেখাই সেগুলি — কম শোনা গান, অসাধারণ, যেমন কথা তেমনি সুর। ‘বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ, নবযুগ ওই এলো ওই’। এছাড়া ছিল, ‘আজ রক্ত নিশিভোরে একি এ শুনি ওরে/ মুক্তি কোলাহল বন্দী শৃঙ্খলে’ আর ‘টলমল টলমল পদভরে বীরদল চলে সমরে’।
ডিসেম্বরের একটানা প্রায় সপ্তাহব্যাপী সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের অনুষ্ঠানে প্রতিবারই বরাদ্দ থাকত ছুটুমার নির্দেশে কোনো না কোনো রবীন্দ্র-নাটক – বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, ‘তাসের দেশ’ বা ‘ফাল্গুনী’।
‘তাসের দেশ’ হাদিস পার্কে একবার হয়েছে, পরবর্তীকালে খুলনার দক্ষিণডিহিতে অসংখ্যবার।
কলকাতা থেকে এসেছেন খ্যাতনামা শিল্পী গৌতমদা, গৌতমবরন অধিকারী। তাঁকে ঘিরে আমাদের মজাদার সব মহড়া, নাচ গান, দুই-ই একই সঙ্গে চলছে। গৌতমদার মতো অমায়িক শিল্পীর সুবাদে আমাদের ঝানু ও কাঁচা শিল্পীদের মধ্যে বিভেদ চটে গেছে। নাটকের গান শেখানো ও রাজপুত্রের সংলাপ ও গান তাঁরই। নাচ করছেন সুশীল সাহা, শেখাচ্ছেনও তিনি।
‘তাসের দেশ’-এর যাবতীয় সাজসজ্জা তৈরি করেছিলেন মৃত্যুনদা।
রুইতনের সংলাপে ছিলেন আমাদের দাদা অরূপরতন ঘোষ, হারিয়ে গেছেন অকালে। অসাধারণ খোল বাজাতেন, আবৃত্তি করতেন, শিল্পীসত্তা ছিল ষোলো আনা। আমি কীভাবে যেন হরতনীর সংলাপ বলার সুযোগ পেয়ে যাই; গানগুলি করেছিলেন আমার দিদি অপরাজিতা ঘোষ। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা, আর আমাদের পিসিদের গানের শিক্ষা মিলে তিনি আমার বরাবরের রোল-মডেল।
মাধব রুদ্র ছিলেন সদাগরপুত্রের ভূমিকায়, আর অন্যান্য ভূমিকায় অসংখ্য প্রতিভাময় শিল্পী, স্বপন ঘোষাল, শংকর মল্লিক, সুদেবদা, রিনাদি, রাণীদি, দীপাদি, সত্যজিৎ রায় মজুমদার, মীনা মিজান ভাই, হাসান তারেক — খেলাঘরের কর্মী, আরো অনেকে। এভাবে বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার মানুষকে একই মঞ্চে কিছু সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আনন্দ ও দুঃখের ধার একই সঙ্গে বুকে ধারণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন ছুটুমা।
১২
‘আমাদের এ দেশের সমস্যা কী জানিস? প্রাণ নয় — মূর্খামি।’ তো এই মূর্খামিকে বিজ্ঞানমনস্কতার স্তরে ও চেতনার স্তরে পাল্টাবার, মানুষকে আরো যুক্তিবাদী, মানবিক, আরো সচেতন, আরো দায়িত্বশীল করে তোলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে হাতিয়ার হিসেবই ব্যবহার করেছেন এঁরা দুজন।
আর সেখানেই রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটক হয়ে উঠেছে অপরিহার্য।
১৯৮৯ সালে খুলনার মহেশ্বরপাশায় আনকোরা নতুন শিল্পীদের নিয়েই, এবং তারপরে হাজার হাজার জনতার সামনে ১৬ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানে হাদিস পার্কে ১৯৯২ সালে এবং পরবর্তীকালে দক্ষিণডিহিতে গ্রাম ও শহরের শিল্পীদের একত্র করে ‘ফাল্গুনী’ অভিনীত হয়েছে বারবার। এটা আমাদের জীবনে তাই একটি ‘রেকারিং থীম’। মৃত্যুর ভেতর, জীবনকে নতুন করে আবিষ্কার। রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটা চেতনাগম্য করতে পারেন, অনায়াসে।
প্রজন্মান্তরে, অনেক পরে ছুটুমারা অবসর নেবার পরে যখন গ্রামে শুরু করলেন তাঁদের নতুন জীবন, গ্রামের ছেলেমেয়েরাও মেতে যায় এই নাটকে।
পুরনো উল্লিখিত শিল্পীরা ছাড়াও নতুন প্রজন্মের নতুন শিল্পীদের মধ্যে ছিল, সায়ন হাসান, কায়সার আলী, মিন্টু কিবরিয়া, অরুণ দাস, রাজীব কর্মকার, লাল্টু পাল, সূর্যদীপ্ত মজুমদার প্রমুখ আরো অনেকে। ছিলেন বিষ্ণুদা, প্রবীরদা, উজ্জ্বল, বাচ্চুকাকা (হাসান আজিজুল হকের ভাই, এখন যিনি ছুটুমার স্থানীয় সব ধরণের সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেকে অসামান্য ধৈর্য আর শক্তি দিয়ে নিয়োজিত রেখেছেন)। আর পেছন থেকে অন্ধ বাউলের গানের কণ্ঠ বারবারই দিয়েছিলেন খুলনার বিখ্যাত শিল্পী সাধন ঘোষ, আমাদের সাধন কাকু। তাঁর মেয়ে সোমা আসে গান করতে। থাকে পুরনো নতুন আরো অনেকেই। সমবেত গানের দলের নেতৃত্বও দিতেন সাধন কাকু, প্রায়শ। আর দিয়েছেন গৌতমদা — সেই ১৯৯২ সালে। সে-বার হাদিস পার্ক মেতে উঠেছিল এঁদের নাচ গান সংলাপে।
বলতে ভুলে গেলেও বলে ফেলি, পয়লা বৈশাখের মতো, আমরা ছুটুমার বাড়িতে পয়লা আশ্বিনও উদ্যাপন করতে শিখেছি। খুবই ভোরে হাজির হতাম তাঁর ফ্ল্যাটের ছাদে। খুলনার বিখ্যাত সঙ্গীতসাধক ও সুরকার সাধন সরকার ছিলেন মধ্যমণি। তাঁর ললিত কণ্ঠে ভৈরবীর সুরে আরম্ভ হত গান। চলত সমবেত, দ্বৈত ও একক গান, এবং কবিতা। ছোট থেকে বড় সকলে অংশ নিত। আমাদের পড়তে হত কমলা-হলুদ শাড়ি — শরতের সোনালি রোদের সঙ্গে মিলিয়ে। তারপর এন্তার লুচি আলুর দম ইত্যাদি খাওয়া। ভোরের ‘structured’ গানের আসর শেষে বেলায় শুরু হত ‘unstructured’ গান — সেখানে গণসংগীতও থাকত। ছুটুমা এক পর্যায়ে ছোটদের হুল্লোড়কে তাদের নিজেদের গতিতে চলতে দিতেন।
ফিরে আসি ‘ফাল্গুনী’তে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে আমরা যা বুঝি, সেই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই নাটকের তাৎপর্য আরো বেশি। মৃত্যুর ছদ্মবেশে জীবন ফিরে ফিরে আসে। জরা-কে পরাস্ত করে মানুষের অদম্য প্রাণশক্তি। এমন একটা মোটা দাগের কথা আছে এতে। প্রতিবারই আমার রোম খাড়া হয়ে উঠত শিহরনে। কী চমক, উত্তেজনা, কী নির্ভার আনন্দ ওই একটি নাটকে।
শেষ করি ‘ফাল্গুনী’র স্পর্শে উজ্জীবিত মানুষ নিয়ে লেখা একটি কবিতা দিয়ে — কবিতাটি ছুটুমা হাদিস পার্কে বিজয় দিবসের কোনো অনুষ্ঠানে পড়িয়ে থাকবেন হয়তো। জীবনকে ভালোবাসার এক চূড়ান্ত মুহূর্তে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মেলবন্ধনে, পনেরো বছর বয়েসে কবিতাটি লেখা। নিজের লেখা বলেই এর কাঁচামির জন্য মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি, ছুটুমা ছাড়া এমন ভাবে কাঁচা হাত দিয়ে কবিতা লেখানোর প্রেরণা কেউ কি আর দিতে পারত!
ওদের দেখেছিলাম;
জীবন্ত ফাল্গুনী ওদের ছুঁয়ে যায় লহমায়
নিটোল, মোহন রোদ্দুরের মতনওরা পারে,
পুঁথি-নক্সার ছায়া কেটে
হেঁটে যেতে —মনে হয়েছিল
বিপুল সর্বনাশা ওদের শোণিতে
রক্ত-জবা ফোটে নিত্যদিনসপ্তরশ্মির চমকপ্রদ আভায় ওরা
রংধনু এঁকে দিতে পারে
আকাশের গায় ।হেসে
ওরা জবরদস্তির হাতকড়া ভাঙতে পারে
নিমেষে
ব’লে — শত্রু, আমরা অনন্তের মতো
ছেয়ে আছি আকাশের নীলে
বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে,
ফুলের স্তবকে
ও কানাগলির মোড়ে;
ছেয়ে আছি দশদিকে,
জীবনের সত্তার মতো,
তার অস্থি-মজ্জায়
ধমনীর প্রবাহ-আবেশে ।শরতের মাজা পাতার মতো
এক ঝলক মুখে ওদের
ফোটে তারা, সূর্যরশ্মি,
ভালোবাসার গনগনে লিপি
প্রহরে প্রহরে।
Have your say
You must be logged in to post a comment.
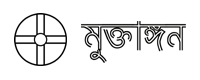







৩ comments
Pingback: ‘পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে’ | আনন্দময়ী মজুমদার
কাজী চপল - ৩ এপ্রিল ২০১৬ (৩:৩০ অপরাহ্ণ)
হাদিস পার্কে তাশের দেশ নাটকে রাজার চরিত্রে এ অধম অভিনয় করেছিল। আমি খুলনা ছেড়েছিলাম ১৯৯১তে আর দিদি দক্ষিণদিহিতে চলে যাবার পর আর যোগাযোগ হয়নি। দিদি আছেন আমার মস্তিস্কের স্নায়ুতে, আমার চেতনায় আর যাবতীয় মূল্যবোধে
-(http://mediakhabor.com/?p=22698)
আনন্দময়ী - ১৬ এপ্রিল ২০১৬ (৮:৪৭ অপরাহ্ণ)
আমি সে সময় ক্লাস ৯-এর ছাত্রী যত দূর মনে পড়ে। হাদিস পার্কে মুক্তি মজুমদারের নির্দেশনায় সেই প্রথম তাসের দেশ মঞ্চস্থ হল। মনে আছে সে সব চপল দা। ভালো থাকবেন।